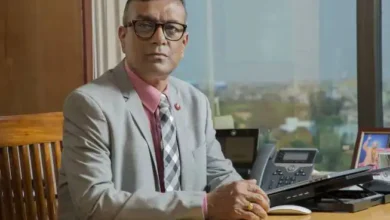বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন হয় কৃষ্ণনগর থেকে— এটাই প্রচলিত মত। নদিয়া-রাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গার আরেক রূপ জগদ্ধাত্রীর আরাধনা কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে প্রথম শুরু করেন। সেই থেকেই শুরু। তারপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র বাংলার মানুষ দেবী জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে জেনেছেন। কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি হুগলির চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো বিশেষ আড়ম্বরের সাথে হয়ে থাকে।
চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের পশ্চাতেও কৃষ্ণনগরের সাথে যোগসূত্রতা পাওয়া যায়। চন্দননগর এবং কৃষ্ণনগর এই দুই নগরের ভৌগোলিক দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। আজ বাংলার একাধিক জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন হলেও, চন্দননগর এবং কৃষ্ণনগরে সবচাইতে বেশি আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটি শহর ধারাবাহিকভাবে তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত জগদ্ধাত্রী পুজো মহাসমারহে পালন করে আসছে।

বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজো প্রচলনের ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করে দেখা যাক। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে শূলপাণি কালবিবেক গ্রন্থে কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পুজোর উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া পূর্ববঙ্গের বরিশালে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত জগদ্ধাত্রীর একটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রত্নবিভাগে সেই প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত রয়েছে। নদিয়ার শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবমন্দিরের গাত্রে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি রয়েছে। শান্তিপুরের এই মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের অনেক আগেই নির্মিত হয়।
অনুমান নদিয়া-রাজ রুদ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণের জননী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আরেকটি মত হল নদিয়া-রাজ রাঘব রায় এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। আরেকটি মন্দির হল রাঘবেশ্বর শিবমন্দির, যার গাত্রেও জগদ্ধাত্রীর মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে দিগনগরে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজা রাঘব রায় এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মন্দিরটি ১৫৯১ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং নদিয়া-রাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের অনেক আগে থেকেই বাংলায় দেবী জগদ্ধাত্রী সম্পর্কে মানুষের ধারনা ছিল।

তাহলে প্রশ্ন হল জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা কী? সেটি এবার দেখা যাক। আসলে আমরা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তক না বলে যদি প্রচারক বলি তাহলে মনে হয় বিভ্রান্তি কিছুটা কমবে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব আলীবর্দী খাঁ-র রাজত্বকালে মহাবদজঙ্গ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নজরানা দিতে অপারগ হন। অতঃপর নবাবের বাহিনী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যায়। এর কয়েক মাস পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী নায়েব রঘুনন্দন মিত্রের ব্যবস্থাপনায় নবাব দরবারে অনাদেয় করের প্রায় অর্ধেক অংশ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হলে কৃষ্ণচন্দ্র আলীবর্দীর কারাগার থেকে মুক্তি পায়।
মুক্তিলাভের পর কৃষ্ণচন্দ্র নদীপথে কৃষ্ণনগরে ফিরছিলেন। সেই সময় নদীঘাটে তিনি বিজয়াদশমীর বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝতে পারেন যে, সেই বছর দুর্গাপুজোর কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র কারাগারে বন্দি থাকায় সেই বছর কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো হয়েছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। নৌকাতেই ঘুমিয়ে পড়েন। তখন মহারাজার স্বপ্নে মা দুর্গা জগদ্ধাত্রী রূপে আবির্ভূত হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে পরবর্তী শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে একই দিনে জগদ্ধাত্রীরূপী দেবী দুর্গার পুজো করার আদেশ দেন। তাহলে চার দিনের দুর্গাপুজোর সমান পুণ্যলাভ সম্ভব। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নে দেখা দেবীর মতো জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে পরবর্তী শুক্লা নবমী তিথিতে একই দিনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো দেন।
সেই বছরই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির নাটমন্দিরে জগদ্ধাত্রী পুজো করেন। অনুমান সালটি ছিল ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি মতও রয়েছে যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আলীবর্দী খাঁ নয়, নবাব মীর কাশিমের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরছিলেন। উল্লেখ্য, নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে ছিলেন জগৎ শেঠ, যাঁর আবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র।

মসনদে বসার পর তাই স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাশিম সেই ক্ষমতাচক্রকে ভাঙতে উদ্যোগী হন। তিনি ১৭৬৩ সালে জগৎ শেঠকে হত্যা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রকেও বন্দী করে তাঁর নতুন রাজধানী মুঙ্গেরে নিয়ে যান। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদান্যতায় কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পান। অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক জগদ্ধাত্রী পুজো সূচনার ক্ষেত্রেও দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়কাল পাওয়া যাচ্ছে।
হুগলির চন্দননগরে আবার জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তক হিসেবে জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নামটি সামনে আসে। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অতি ঘনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন ফরাসি সরকারের দেওয়ান। প্রচলিত একটি মত হল— তিনি কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো দেখে মুগ্ধ হন এবং চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জ চাউলপট্টির নিচুপাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেন। তবে এখানে একটি গরমিল রয়েছে, সেটি হল— কৃষ্ণনগরে যদি জগদ্ধাত্রী পুজো প্রবর্তিত হয়েছিল ধরা হয় ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের পরে কোনো এক সময়, তাহলে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন তো জীবিতই ছিলেন না।
১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দেই তিনি প্রয়াত হন। তাহলে কিভাবে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রবর্তন করলেন? এ প্রশ্নটিও থেকে যায়। আবার এমনও মনে করা হয় যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রাজা গিরীশচন্দ্র রায় (১৮০২-১৮৪১ খ্রি.) জগদ্ধাত্রী পুজো প্রবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। আসলে বোঝাই যাচ্ছে যে, বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় এখনো অস্পষ্ট। জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে এর অনেক কিছু নিয়েই এখনো দ্বিমত রয়েছে। এ বিষয়ে তাই আরও সুগভীর গবেষণা প্রয়োজন।
লেখক: অধ্যাপক, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া।